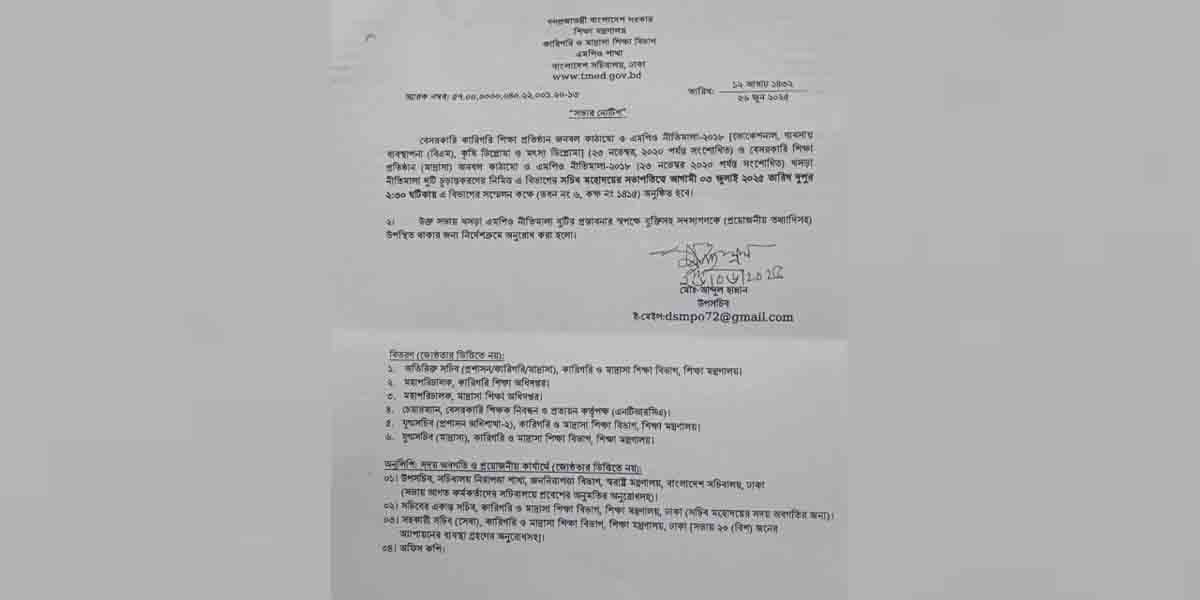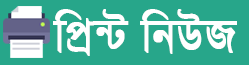
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। নানা মত ও পথের মানুষ তাদের নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রতিনিয়ত রাজপথে সক্রিয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। সম্প্রতি নির্বাচন পদ্ধতির ধরন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন বেশ সরগরম। বাংলাদেশে বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতি হলো ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) বা সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পান, তিনিই নির্বাচিত হন। এমন নির্বাচন পদ্ধতি স্থিতিশীল সরকার গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বিধায় বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো এ বিদ্যমান পদ্ধতির পক্ষে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণ অধিকার পরিষদ, এনসিপিসহ বেশকিছু ছোট রাজনৈতিক দল প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে জোরালো দাবি তুলেছে। এ পদ্ধতিতে ভোটের শতকরা হার বিবেচনা করা হয় বিধায় ছোট দলগুলোর সংসদে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এখন নিরূপণের বিষয় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের যৌক্তিকতা
নির্বাচনে পিআর পদ্ধতিঃ-
প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) হলো এমন নির্বাচন পদ্ধতি যেখানে জনগণ প্রার্থীর পরিবর্তে রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের দেয়া ভোটের অনুপাত অনুযায়ী সংসদ বা আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করে। সহজভাবে বললে পিআর পদ্ধতিতে যে দল যত শতাংশ ভোট পায়, সে দল সংসদে তত আসন পায়। যেমন বাংলাদেশে ৩০০টি সংসদীয় আসনে পিআর পদ্ধতিতে কোনো দল ৩০ শতাংশ ভোট পেলে, সে দল সংসদে ৯০টি আসন পাবে: ১০ শতাংশ ভোট পেলে ৩০টি আসন পাবে। নেদারল্যান্ডস, ইসরায়েল, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি (আংশিক পিআর), শ্রীলংকাসহ বিশ্বের বেশকিছু দেশে পিআর পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতির দুর্বলতা কাটাতে এবং সংসদে অতিরিক্ত খণ্ড-বিখণ্ডতা এড়িয়ে কার্যকর জোট সরকার গঠনে অনেক দেশ ইলেকটোরাল থ্রেশল্ড বা সর্বনিম্ন ভোট পাওয়ার বিধানও রেখেছে। সর্বনিম্ন ভোট পাওয়ার বিধান থাকার কারণে সংসদে অতি ছোট বা উগ্রবাদী দলের অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব হয় এবং একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের পথ সুগম হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সর্বনিম্ন ভোট পাওয়ার হার (থ্রেশল্ড); জার্মানিতে ৫ শতাংশ; ইসরায়েলে ৩ দশমিক ২৫, তুরস্কে ৭ (আগে ছিল ১০ শতাংশ), রাশিয়া ৫. নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেনে ৪ শতাংশ।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাঃ-
পিআর পদ্ধতিতে প্রতিটি দলের আসনপ্রাপ্তি তাদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্ধারিত হওয়ায় সব নাগরিকের মতামতের মূল্যায়ন হয়; ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়; রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভোটার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা বাড়ে, তবে এ প্রতিযোগিতার নেতিবাচক দিকও আছে; একক দলের আধিপত্য কমে; সরকার গঠনে নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত একটি জোট সরকার গঠনের পরিবেশ তৈরি হয়। এ সুবিধাগুলো গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুললেও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ পদ্ধতির পেছনে এক ধরনের ভৌতিক বাস্তবতা বিরাজমান, যা দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন-
প্রার্থী নয়, দলকে ভোট দেয়ার সমস্যাঃ-
পিআর পদ্ধতিতে ভোটার সরাসরি প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে দলকে দেয়ায় দল তার ইচ্ছামতো অনুগত, বিত্তশালী বা নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যক্তিকে সংসদে মনোনয়ন দেয়। ফলে জনগণের প্রতি প্রার্থীর কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না এবং প্রার্থীর সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র খুবই দুর্বল হয়; দলীয় আনুগত্য, ক্ষমতার দাপট ও টাকার খেলা প্রবল হয়ে ওঠে: সৎ, যোগ্য, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ হ্রাস পায়। সংসদে এমন মানুষের প্রাধান্য দেখা দেয় যাদের মধ্যে নৈতিকতা বা জনসেবার চিন্তা নেই, বরং ক্ষমতা রক্ষা ও নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।
রাজনীতিতে দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাবঃ-
বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থায় এখনো অর্থের বিনিময়ে ভোট কেনাবেচার সংস্কৃতি বিদ্যমান। পিআর পদ্ধতিতে এ পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে। FPTP পদ্ধতিতে ভোট কেনা-বেচা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্থানীয় দুর্নীতি, কিন্তু এ পদ্ধতিতে এ দুর্নীতি দলীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ সংস্কৃতির কারণে দলে বিত্তবান প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়ার প্রবণতা দেখা দেবে; নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব বাড়বে; সৎ নেতৃত্ব অসৎ নেতৃত্বের কাছে পরাজিত হবে: সামাজিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হবে: সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা বাড়বে: রাজনীতিতে মতাদর্শ প্রচারের সংস্কৃতির জায়গায় নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, যা মানুষের মুক্তির পথকে একেবারে রুদ্ধ করে দেবে। সর্বোপরি রাজনীতি একটি জনহিতকর পেশা থেকে ব্যবসায়ী হিসেবে পরিগণিত হবে।
মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকাঃ-
বাংলাদেশের অনেক গণমাধ্যম তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে মনগড়া তথ্য প্রচার করে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনে মিডিয়ার প্রভাব আরো বাড়বে; কোনো দলকে ক্ষমতায় আনতে বা হটাতে মিডিয়া একতরফা প্রচারে জড়াবে; মানুষ বিভ্রান্ত হবে এবং তথ্যপ্রবাহে প্রভাবিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেবে; এতে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।
জোট সরকারের দুর্বলতাঃ-
পিআর পদ্ধতিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কঠিন হওয়ায় জোট সরকার গঠন করতে হয়। জোট সরকার গঠন সময়সাপেক্ষ ও দুর্বল হয়ে থাকে। ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসে সরকার গঠনে ২৭১ দিন সময় লেগেছিল; ইসরায়েলে সংসদে স্থিতিশীলতা না থাকায় ২০১৯-২২ সময়ের মধ্যে পাঁচবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ঘনঘন নির্বাচন আয়োজন করা কঠিন এবং ব্যয়বহুল। এছাড়া জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জোটভিত্তিক মতানৈক্যের কারণে আইন প্রণয়ন ব্যাহত হতে পারে অথবা আইন প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হতে পারে।
সংসদে ছোট দলগুলোর মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবঃ-
বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এ দলগুলো রাজনীতির মাঠে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও মিডিয়ায় তাদের আস্ফালন যথেষ্ট লক্ষণীয়। এদের মধ্যে কিছু দল উগ্র ও চরমপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, যা গণতান্ত্রিক সহনশীলতার জন্য একটি বড় হুমকি। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টিত হয় বিধায় ক্ষুদ্র বা উগ্রবাদী দলগুলো সংসদে প্রবেশের সুযোগ পেতে পারে। এসব দল সংসদে বড় দলগুলোর সঙ্গে আপস করে নিজেদের স্বার্থে আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমনকি প্রস্তাবিত আইন বাধাগ্রস্তও করতে পারে। ফলে সংসদের কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি ও অসংগতি সৃষ্টি হতে পারে।
প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টিঃ-
পিআর পদ্ধতির আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো এর প্রশাসনিক জটিলতা। ভোট গণনা, আসন বণ্টন এবং ফলাফল নির্ধারণ একটি দীর্ঘ, জটিল ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া হওয়ায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় এ ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা অতিরিক্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে, যা বাজেট ঘাটতি ও রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে নির্বিচারে দলীয়করণের সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকায় অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হতে পারে
পিআর পদ্ধতিতে সম্ভাব্য লাভ ও ক্ষতিঃ-
বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে কার লাভ হবে, কার ক্ষতি-তা নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ, আশঙ্কা ও প্রত্যাশা। এ পদ্ধতিতে আওয়ামী লীগ সদ্যবিদায়ী শাসক দল হিসেবে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বলে
অনেকে মনে করেন। দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার সুবাদে প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে দলীয়করণ, অর্থিক সামর্থ্য ও প্রভাবের দিক দিয়ে অনেকটাই শক্তিশালী অবস্থানে। যদি তারা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনে নিজেদের প্রতীক ও ব্যানার ব্যবহারের সুযোগ পায়, তবে ভোট কেনাবেচা ও প্রভাব বিস্তারের সংস্কৃতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান নিশ্চিত করতে পারবে। যদি তারা বিচারের সম্মুখীন হয় এবং নিজেদের প্লাটফর্ম ব্যবহারে ব্যর্থ হয়ে অন্য কোনো যৌথ প্লাটফর্ম বা ভিন্ন ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নেয়, তবে সেই প্লাটফর্মই আওয়ামী লীগের সাজানো রাষ্ট্রযন্ত্র, আর্থিক সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক লাভবান হবে। অনেকে আশঙ্কা করছেন, আওয়ামী লীগের বিপুল আর্থিক সামর্থ্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনে ভোট কেনাবেচার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিতে পারে। এ পদ্ধতিতে এককভাবে সরকার গঠনে মোট ১২ কোটি ৩৭ লাখ ভোটের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ভোটের প্রয়োজন হবে। ভোট কেনাবেচার সংস্কৃতিতে যদি একেকটি ভোটের ‘মূল্য’ ১ হাজার টাকা ধরা হয় ৬ কোটি ভোট ক্রনয়ে ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার সামর্থ্য কেবল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা দলটির পক্ষেই সম্ভব বলে ধারণা করা হয়। অন্যান্য দিক থেকে দেখা গেলে, পিআর পদ্ধতির পক্ষে। থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিছু বিতর্কিত ও হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দলের অবস্থানও প্রশ্নবিদ্ধ। ইসলামপন্থী কিছু দল, অতি-জাতীয়তাবাদী দল কিংবা নব্য রাজনৈতিক শক্তিগুলো যেভাবে
পিআর পদ্ধতির পক্ষে সুর মিলিয়েছে, তা নিয়ে জনমনে সন্দেহ রয়েছে। কেউ কেউ একে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন-যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনার শক্তিগুলোকে দুর্বল করে পুনরায় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা। আবার জাতীয় রাজনীতিতে এনসিপির মতো কিছু নবীন দলের নেতা যেমন ৩০০ আসনে বিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন, তা বাস্তবতার আলোকে অনেকের কাছে হাস্যকর বা বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একইসঙ্গে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণ অধিকার পরিষদ এবং কিছু বিতর্কিত ব্যক্তির পিআর পদ্ধতির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে তুলেছে। এখন রাজনীতিতে একটি বড় প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে দুর্বল সরকার গঠন হলে বা রাজনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করলে কিংবা পুনরায় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হলে কার লাভ কার ক্ষতি?
পরিশেষে বলা যায়, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি যেমন কিছু ছোট দলের জন্য আশার আলো হতে পারে, তেমনি গণ-অভ্যুত্থানে পতিত আওয়ামী লীগের জন্য হতে পারে ক্ষমতায় ফেরার নতুন কৌশল। তাছাড়া রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত সমাজে উগ্রবাদী ও সুবিধাবাদী দল সংসদে ঢুকে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকার গঠন জটিল হতে পারে। অতএব এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের আগে জাতীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক ভারসাম্য ও জনমতের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন অপরিহার্য।

 মোফাক্কারুল ইসলাম (মিশন)
মোফাক্কারুল ইসলাম (মিশন)